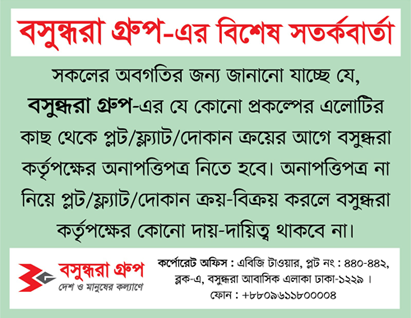ক্লাউডফ্লেয়ারের একটি ভুলে কীভাবে থমকে গেল বিশ্বের ২০% ওয়েবসাইট । সমুদ্রের তলদেশ থেকে আপনার মোবাইল পর্যন্ত বাংলাদেশের ইন্টারনেট অবকাঠামোর অদৃশ্য যাত্রাপথ ।
ইন্টারনেটের হৃৎস্পন্দন যখন থমকে যায়

মোঃ রেজাউল করিম রাজু : গত ১৮ নভেম্বর বিশ্ব প্রযুক্তির ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে গেল। সাধারণ ব্যবহারকারীদের কাছে মনে হয়েছিল হয়তো তাদের ওয়াইফাই বা মোবাইল ডেটায় সমস্যা হচ্ছে, কিন্তু পর্দার আড়ালে তখন ঘটে যাচ্ছিল এক মহাবিপর্যয়। বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশেরও বেশি শীর্ষস্থানীয় ওয়েবসাইট যার মধ্যে ছিল জনপ্রিয় ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, ডিসকর্ড, এবং হাজার হাজার সংবাদমাধ্যম হঠাৎ করেই ‘অফলাইন’ হয়ে যায়। ব্রাউজারে ভেসে ওঠে ‘500 Internal Server Error’ বা ‘502 Bad Gateway’।
এই ডিজিটাল স্থবিরতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল একটি মাত্র নাম ‘ক্লাউডফ্লেয়ার’। ইন্টারনেটের ট্রাফিক পুলিশ হিসেবে পরিচিত এই প্রতিষ্ঠানটির একটি সামান্য ত্রুটি কীভাবে বিশ্বজুড়ে ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করল? আর এই বিশাল জালের অপর প্রান্তে থাকা বাংলাদেশে, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে ইন্টারনেট কীভাবে একজন প্রান্তিক গ্রাহকের হাতে পৌঁছায়? আজকের এই বিশেষ প্রতিবেদনে আমরা অনুসন্ধান করব ইন্টারনেটের সেই অদৃশ্য অলিগলি।
কেন ২০ শতাংশ ইন্টারনেট উধাও হলো?
ইন্টারনেটকে আমরা একটি বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা ভাবলেও, বাস্তবতা হলো আধুনিক ওয়েবের বড় অংশ গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল। ক্লাউডফ্লেয়ার হলো তেমনই এক জায়ান্ট, যারা বিশ্বের কোটি কোটি ওয়েবসাইটের ‘সিডিএন’ (কন্টেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক) এবং নিরাপত্তা দেয়াল হিসেবে কাজ করে।
১৮ নভেম্বর আসলে কী ঘটেছিল? : ইন্টারনেট দুনিয়ায় গুজব রটেছিল এটি হয়তো কোনো বড় হ্যাকার গ্রুপের কাজ। কিন্তু ক্লাউডফ্লেয়ারের সিইও ম্যাথিউ প্রিন্স এবং তাদের অফিশিয়াল ব্লগের তথ্য অনুযায়ী, এটি ছিল সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ একটি যান্ত্রিক ত্রুটি। ক্লাউডফ্লেয়ার তাদের গ্রাহকদের নিরাপত্তা দিতে ‘বট ম্যানেজমেন্ট’ নামে একটি সিস্টেম ব্যবহার করে, যা ক্ষতিকর রোবট বা বট আটকাতে সাহায্য করে। ১৮ নভেম্বর বিকেলে ইঞ্জিনিয়াররা এই সিস্টেমে একটি ছোট আপডেট বা ‘কনফিগারেশন চেঞ্জ’ পুশ করেন। কিন্তু বিপত্তি ঘটে সেখানেই। একটি ভুলের কারণে কনফিগারেশন ফাইলটির আকার (সাইজ) প্রত্যাশার চেয়ে বহুগুণ বেড়ে যায়।
এই বিশাল ফাইলটি যখন বিশ্বজুড়ে ক্লাউডফ্লেয়ারের হাজার হাজার সার্ভারে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সার্ভারের প্রসেসরগুলো তা লোড করতে ব্যর্থ হয় এবং ক্র্যাশ করে। ফলাফল সার্ভার ডাউন, ইন্টারনেট অচল। প্রায় ৫ ঘণ্টা চেষ্টার পর রাত ৯ টার দিকে (বাংলাদেশ সময়) পুরনো ফাইলে ফিরে গিয়ে (রোলব্যাক) পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়। এটি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, আধুনিক ইন্টারনেট ব্যবস্থা কতটা ‘সিঙ্গেল পয়েন্ট অফ ফেইলিউর’ বা একক নির্ভরতার ঝুঁকিতে আছে।
ক্লাউডফ্লেয়ারের বিকল্প মার্কেট লিডার কারা?
এই ঘটনার পর প্রশ্ন উঠছে, আমরা কি অনেক বেশি ক্লাউডফ্লেয়ারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি না? তবে বাজারে তাদের সমকক্ষ আরও কিছু শক্তিশালী খেলোয়াড় রয়েছে, যারা ব্যাকআপ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে:
১. আকামাই : সিডিএন জগতের এই পুরনো ও অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানটি ব্যাংকিং এবং নিরাপত্তা খাতের জন্য অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।
২. ফাস্টলি : রিয়েল-টাইম ডেটা প্রসেসিংয়ের জন্য বিখ্যাত, যদিও ২০২১ সালে তাদেরও একটি বড় বিপর্যয় হয়েছিল।
৩. অ্যামাজন ক্লাউডফ্রন্ট : অ্যামাজনের নিজস্ব এই সেবাটি বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ কন্টেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক।
৪. গুগল ক্লাউড সিডিএন: গুগলের শক্তিশালী ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্যবহার করে তারা দ্রুত উঠে আসছে।
মহাসমুদ্রের তলদেশ থেকে বাংলাদেশে যে ভাবে ঢোকে ইন্টারনেট
অনেকের ধারণা ইন্টারনেট আকাশ বা স্যাটেলাইট দিয়ে আসে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশের ৯৫ শতাংশেরও বেশি ডেটা বা ইন্টারনেট আসে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে বিছানো অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে। একে বলা হয় সাবমেরিন ক্যাবল।
বর্তমানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলস পিএলসি (বিএসসিপিএলসি) এর মাধ্যমে দুটি প্রধান সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে যুক্ত:
- সি–মি–উই ৪ (সাউথ ইস্ট এশিয়া-মিডল ইস্ট-ওয়েস্টার্ন ইউরোপ) : এটি কক্সবাজারের ঝিলংঝা ল্যান্ডিং স্টেশনে যুক্ত। এটি আমাদের প্রথম লাইফলাইন।
- সি–মি–উই ৫ : এটি পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় ল্যান্ড করেছে। এটি বর্তমানে বাংলাদেশের ব্যান্ডউইথের সিংহভাগ জোগান দেয় এবং এর ক্ষমতা অনেক বেশি।
- (উল্লেখ্য, সি–মি–উই ৬ নামের তৃতীয় ক্যাবলটি ২০২৬ সালের মধ্যেই সম্পূর্ণ অপারেশনে আসার প্রক্রিয়ায় রয়েছে, যা আমাদের সক্ষমতা বহুগুণ বাড়াবে)
বিকল্প পথ আইটিসি (ইন্টারন্যাশনাল টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবল) :
সাবমেরিন ক্যাবল যদি কখনো কাটা পড়ে, তখন ব্যাকআপ হিসেবে কাজ করে এটি ভারতের বর্ডার (বেনাপোল) দিয়ে মাটির নিচ দিয়ে আসা ফাইবার ক্যাবল। সামিট কমিউনিকেশনস, ফাইবার অ্যাট হোমের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো ভারতের টাটা বা এয়ারটেলের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে আমাদের গ্লোবাল ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত রাখে।
ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক ল্যান্ডিং স্টেশন থেকে আপনার এলাকা
কক্সবাজার বা কুয়াকাটায় ইন্টারনেট তো এল, কিন্তু সেখান থেকে ঢাকায় বা আপনার মফস্বল শহরে পৌঁছায় কীভাবে? এখানে কাজ করে একটি জটিল কিন্তু সুশৃঙ্খল সাপ্লাই চেইন।
ধাপ ১: এনটিটিএন (পরিবহনের দায়িত্ব) : ব্যান্ডউইথ পরিবহনের মহাসড়ক হলো এনটিটিএন (ন্যাশনওয়াইড টেলিকম্যুনিকেশন ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক)। সামিট বা ফাইবার অ্যাট হোমের মতো এনটিটিএন লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানগুলো মাটির নিচ দিয়ে সারা দেশে ফাইবার অপটিকের হাজার হাজার কিলোমিটার জাল বিছিয়ে রেখেছে। এরা ল্যান্ডিং স্টেশন থেকে ব্যান্ডউইথ বহন করে ঢাকায় বা বিভিন্ন জেলায় নিয়ে আসে।
ধাপ ২: আইআইজি (পাইকারি বিক্রেতা) :
ব্যান্ডউইথ ঢাকায় আসার পর তা আইআইজি (ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে) প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে যায়। আইআইজি হলো ইন্টারনেটের পাইকারি বিক্রেতা (যেমন ম্যাঙ্গো, বিটিসিএল)। তারা গ্লোবাল ট্রাফিক কন্ট্রোল করে এবং আইএসপি কাছে ব্যান্ডউইথ বিক্রি করে।
ধাপ ৩: আইএসপি (খুচরা বিক্রেতা) :
আপনার এলাকার ইন্টারনেট প্রোভাইডার বা আইএসপি সেই ব্যান্ডউইথ কিনে নেয়। এরপর তারা রাস্তার পোলে ঝুলানো তারের মাধ্যমে সেই সংযোগ আপনার বাসার ডিস্ট্রিবিউশন বক্স বা ডিবি বক্সে পৌঁছে দেয়।
গ্রাহকের হাতে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি : সবশেষে, কীভাবে এই ইন্টারনেট আপনার ডিভাইসে সক্রিয় হয়? এখানে দুটি প্রধান মাধ্যম কাজ করে:
ক. ব্রডব্যান্ড বা ওয়াইফাই:
আইএসপি ফাইবার ক্যাবলটি আপনার ঘরের ‘ওনু’ ডিভাইসে লাগে। ওনু আলোক সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে রূপান্তর করে রাউটারে পাঠায়। রাউটার সেই সংকেতকে ওয়াইফাই তরঙ্গে বা ল্যান পোর্টের মাধ্যমে আপনার ফোন বা ল্যাপটপে পৌঁছে দেয়।
খ. মোবাইল ইন্টারনেট (সিমের মাধ্যমে):
মোবাইল ইন্টারনেটের প্রক্রিয়াটি আরও বিস্ময়কর।
১. আপনি যখন ডেটা অন করেন, আপনার ফোন বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে নিকটস্থ মোবাইল টাওয়ারের (বিটিএস) সাথে যোগাযোগ করে।
২. মজার বিষয় হলো, টাওয়ার থেকে কিন্তু আর তারবিহীন যোগাযোগ থাকে না। প্রতিটি মোবাইল টাওয়ার মাটির নিচের ফাইবার অপটিক ক্যাবলের মাধ্যমে অপারেটরের (যেমন জিপি বা রবি) মেইন সার্ভারে যুক্ত থাকে।
৩. অপারেটরের সার্ভার আইআইজি হয়ে সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে গ্লোবাল ইন্টারনেটে (যেমন ফেসবুক বা ইউটিউবের সার্ভারে) আপনার রিকোয়েস্ট পাঠায়।
৪. সেখান থেকে ডেটা আবার একই পথে ফিরে এসে টাওয়ার হয়ে আপনার মোবাইলের স্ক্রিনে ভেসে ওঠে।
এই পুরো প্রক্রিয়াটি আমেরিকার সার্ভার থেকে ডেটা এনে আপনার গ্রামের বাড়িতে মোবাইলে দেখানো ঘটতে সময় লাগে চোখের পলকের চেয়েও কম সময় (মিলি-সেকেন্ডে)।
গত দুই দিনের ক্লাউডফ্লেয়ার বিপর্যয় এবং বাংলাদেশের ইন্টারনেট অবকাঠামোর এই ব্যবচ্ছেদ আমাদের একটি সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করায় প্রযুক্তি যত আধুনিক হচ্ছে, আমরা তত বেশি পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হচ্ছি।
বাংলাদেশের ইন্টারনেট ব্যবস্থা এখন আর কেবল শখের বিষয় নয়, এটি অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। সমুদ্রের তলদেশ থেকে শুরু করে মাটির গভীর হয়ে বাতাসের তরঙ্গ পর্যন্ত এই বিশাল কর্মযজ্ঞটি সচল রাখতে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করে যাচ্ছেন হাজারো প্রকৌশলী। ক্লাউডফ্লেয়ারের মতো ঘটনাগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয়, এই অদৃশ্য জালের কোনো একটি সুতো ছিঁড়ে গেলে পুরো পৃথিবী কীভাবে থমকে যেতে পারে। তাই নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিকল্প ব্যবস্থা রাখা এখন আর বিলাসিতা নয়, বরং অপরিহার্য প্রয়োজন।
যোগাযোগ করুন : rajuitnews@gmail.com
মন্তব্য করুন

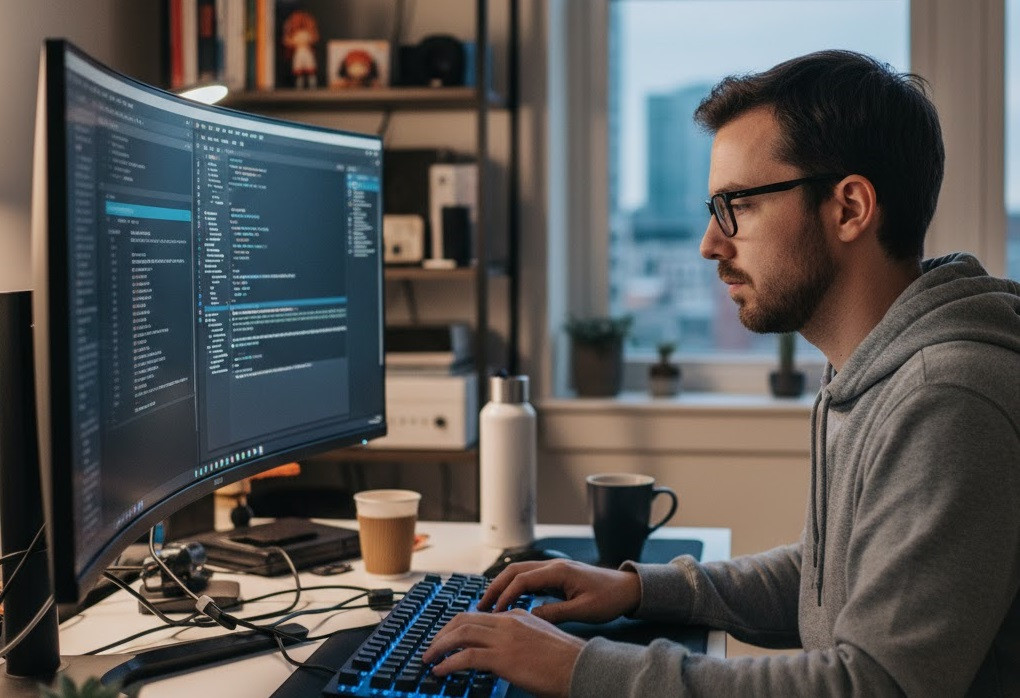 আইটি ডেস্ক
আইটি ডেস্ক



_medium_1762605395.jpg)

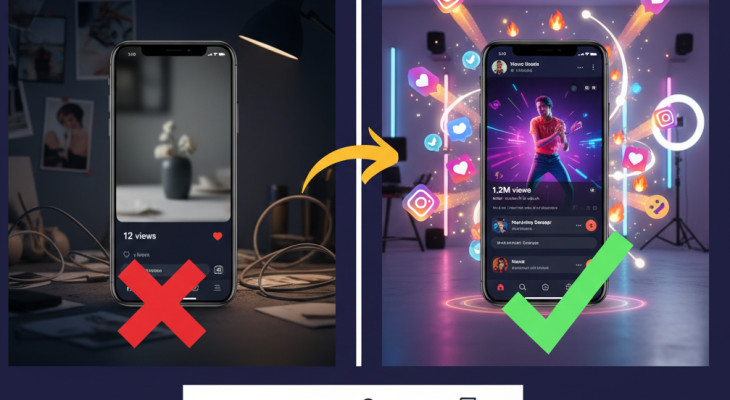
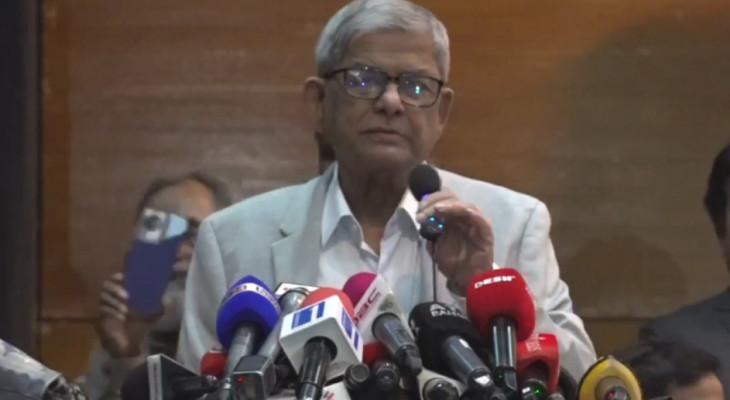

_medium_1763813105.jpg)